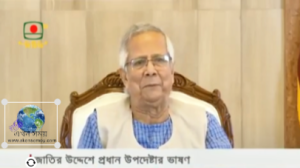ঢাকার আশপাশের নদীগুলো—বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা—ধীরে ধীরে যেন ‘ডাম্পিং জোনে’ পরিণত হচ্ছে। হত্যার পর মরদেহ গায়েব করতে নদীতে ফেলে দেওয়ার ঘটনা গত বছরের তুলনায় এ বছর বেড়েছে বলে নৌ-পুলিশের তথ্য বলছে। ২০২৪ সালে যেখানে মাসে গড়ে ৩৬টি মরদেহ উদ্ধার হতো, চলতি বছরে তা দাঁড়িয়েছে ৪৩টিতে। শুধু সংখ্যাই নয়, শনাক্তহীন লাশের হারও উদ্বেগজনক—উদ্ধার হওয়া মরদেহের প্রায় ৩০ শতাংশেরই পরিচয় মেলে না। এতে অপরাধীরা প্রমাণ নষ্ট করে পার পেয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে, আর এলাকাবাসী ভুগছেন নিরাপত্তাহীনতায়।
গত ২৩ আগস্ট মাত্র ছয় ঘণ্টার ব্যবধানে বুড়িগঙ্গা নদী থেকে চারটি মরদেহ উদ্ধার করে নৌ-পুলিশ। কেরানীগঞ্জের মাদারীপুর ঘাটে যুবকের হাতের সঙ্গে এক নারীর হাত চালের বস্তা দিয়ে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়। একই দিনে মীরেরবাগ এলাকা থেকে উদ্ধার হওয়া নারী ও শিশুর গলায় কাপড় প্যাঁচানো ছিল। স্থানীয়দের ভাষ্য, অধিকাংশ মরদেহের হাত-পা বাঁধা এবং অবস্থাও ছিল খারাপ। নৌপথে চলাচলকারীরা বলেন, ঘনঘন এমন লাশ ভেসে ওঠায় আতঙ্ক ছড়াচ্ছে; কারা, কীভাবে এসব মানুষকে হত্যা করছে—তা নিয়ে গভীর দুশ্চিন্তায় আছেন আশপাশের বাসিন্দারা।
সংখ্যার চিত্র আরও স্পষ্ট। ২০২৪ সালে দেশের বিভিন্ন নদী থেকে মোট ৪৪০টি মরদেহ উদ্ধার করে নৌ-পুলিশ; এর মধ্যে ২৯৯টি শনাক্ত হলেও ১৪১টির পরিচয় মেলেনি। চলতি বছরের প্রথম সাত মাসেই উদ্ধার হয়েছে ৩০১টি মরদেহ, যার মধ্যে ৯২টিই শনাক্ত করা যায়নি। সংখ্যাগুলো প্রমাণ করে, নদীপথে ‘ডাম্পিং’ প্রবণতা বাড়ছে এবং শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় এখনও বড় ঘাটতি রয়ে গেছে।
নৌ-পুলিশের কর্মকর্তাদের মতে, অধিকাংশ মরদেহ দীর্ঘ সময় পানিতে থাকায় পচে-গলে যায়। ফলে আঙুলের ছাপ নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, মুখাবয়বও বিকৃত থাকে। একই সঙ্গে সারা দেশের নদীজুড়ে সার্বক্ষণিক নজরদারির জন্য পর্যাপ্ত ইউনিট ও লজিস্টিক সাপোর্ট নেই। নৌ-পুলিশের ঢাকা অঞ্চলের পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, প্রয়োজনের তুলনায় ইউনিট কম এবং সরঞ্জামেও ঘাটতি আছে; তবে ইউনিট ও লজিস্টিক বাড়াতে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা মনে করেন, নদীতীরের গুরুত্বপূর্ণ ঘাট, ফেরিঘাট, সেতুর নিচ ও নির্জন চরের মতো এলাকাগুলোকে ‘হটস্পট’ ধরে বিশেষ নজরদারি বাড়ানো জরুরি।
অপরাধ বিশ্লেষকেরা বলছেন, কোথায়, কোন সময়ে এবং কীভাবে অপরাধীরা নদীকে ব্যবহার করছে—এটা ডেটা-ভিত্তিকভাবে চিহ্নিত করলেই প্রতিরোধ সহজ হবে। সমাজ ও অপরাধ বিশ্লেষক ড. তৌহিদুল হকের পরামর্শ, অপরাধপ্রবণ স্পটগুলোতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে ২৪ ঘণ্টা মনিটরিং, পানিপথে টহল জোরদার এবং দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে হত্যার রহস্য উন্মোচন অপরিহার্য। না হলে ‘ক্যাচ-মি-ইফ-ইউ-ক্যান’ ধরনের সাহস পেয়ে যাবে অপরাধীরা, যা সামগ্রিক অপরাধপ্রবণতাকে উসকে দিতে পারে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, অপরাধীরা নদী বেছে নেয় মূলত দু’টি কারণে—প্রমাণ নষ্ট করা এবং ঘটনাস্থল থেকে দেহটিকে দ্রুত দূরে সরিয়ে নেওয়া। স্রোত ও জোয়ার-ভাটার কারণে মরদেহ অন্যত্র ভেসে যেতে পারে; এমনকি অন্য থানার অধিক্ষেত্রে উঠে এলে তদন্তও জটিল হয়। ফলে অপরাধের সময়-স্থান-প্রেক্ষাপট পুনর্গঠন কঠিন হয়ে পড়ে। এ বাস্তবতায় আন্তঃথানা ও আন্তঃজেলা সমন্বয় জোরদার, তদন্তের শুরুতেই নিকটবর্তী সিসিটিভি ফুটেজ জব্দ এবং নদীপথের নৌযানগুলোর জার্নাল/লগবুক যাচাই—এসবকে প্রাতিষ্ঠানিক রুটিনে আনা উচিত বলে মত তাদের।
পরিচয় শনাক্তে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ানোও সময়ের দাবি। অনেক ক্ষেত্রে আঙুলের ছাপ অকার্যকর হলে ডিএনএ প্রোফাইলিং-ই ভরসা। এজন্য প্রতিটি নৌ থানা–চৌকিতে মানসম্মত বডিব্যাগ, কোল্ড স্টোরেজ অ্যাকসেস, প্রাথমিক ডিএনএ সংগ্রহের কিট ও প্রশিক্ষিত জনবল প্রয়োজন। নিখোঁজ ব্যক্তিদের তথ্য দ্রুত মিলিয়ে দেখতে একটি কেন্দ্রীয় ডেস্ক—যেখানে পরিবারগুলো ছবি/বিবরণ আপলোড করতে পারে—উদ্ধারকৃত মরদেহ শনাক্তে বড় সহায়ক হবে। নাগরিকদের জন্য ২৪/৭ হটলাইন, এসএমএস/হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ও ওয়েবফর্ম চালুর উদ্যোগও নেওয়া যেতে পারে।
এদিকে নদীপথে দৃশ্যমান উপস্থিতি বাড়াতে নৌ-পুলিশের পাশাপাশি কোস্টগার্ড, নৌবাহিনী ও র্যাবসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অন্যান্য ইউনিটকে সমন্বিত কমান্ডে আনার সুপারিশ এসেছে। দিন-রাত নির্দিষ্ট রুটে কৌশলগত টহল, ড্রোন-সাহায্যিত নজরদারি, লাইভ ম্যাপিং ও জিও-ফেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার—এই ‘মিশ্র মডেল’ কার্যকর হতে পারে। ঘাট-সেতু-টার্মিনালের আলোকসজ্জা, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী নজরদারি টিম ও নদীতীরে কমিউনিটি ওয়াচ পোস্টও অপরাধপ্রবণতা কমাতে ভূমিকা রাখবে।
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে যুক্ত করে নদীতীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, অবৈধ ঘাট-জেটি উচ্ছেদ এবং অন্ধকার-নির্জন স্পটগুলোতে নিয়মিত অভিযানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। কারণ, অপরাধীরা সাধারণত এমন জায়গা বেছে নেয় যেখানে মানুষের বিচরণ কম, আলো কম, সিসিটিভি নেই এবং দ্রুত নৌযান পাওয়া যায়। এসব জায়গা ‘রেড জোন’ হিসেবে চিহ্নিত করে মাসিক রিভিউ মিটিং ও ড্যাশবোর্ডে প্রকাশ করা হলে, মাঠপর্যায়ের ইউনিটেরা লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পনা নিতে পারবে।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি নাগরিকদেরও দায়িত্ব আছে। পরিবারে কেউ নিখোঁজ হলে দেরি না করে থানায় সাধারণ ডায়েরি করতে হবে এবং নৌ থানা–কোস্টগার্ডকে জানাতে হবে। ঘটনাস্থল—যেমন ঘাট বা সেতুর নিচে—গুরুত্বপূর্ণ কোনো সামগ্রী (দড়ি, বস্তা, কাপড়) পড়ে থাকতে দেখলে ‘স্পর্শ না করে’ পুলিশকে খবর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন কর্মকর্তারা। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও নৌযান চালকদেরও সন্দেহজনক নৌযান/ব্যক্তির তথ্য সঙ্গে সঙ্গে জানাতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
সবশেষে বলা যায়, নদীগুলোকে ‘ডাম্পিং জোন’ হতে দিলে জননিরাপত্তা যেমন ঝুঁকির মুখে পড়বে, তেমনি আমাদের নদী-সংস্কৃতি, পর্যটন ও নৌবাণিজ্যের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। দ্রুত ও দৃশ্যমান ব্যবস্থা—হটস্পটভিত্তিক সিসিটিভি, একীভূত টহল, আধুনিক ফরেনসিক ও দ্রুত তদন্ত—নিলে এই প্রবণতা বন্ধ করা সম্ভব। সাধারণ মানুষও চায়, হত্যার পর মরদেহ গায়েব করার সহজ রাস্তা হিসেবে আর কোনো নদীকে যেন ব্যবহার করা না যায়।